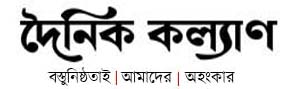মানিক দত্ত
১৯৪১ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির রজত-জুবলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিরূপে নজরুল যে ভাষণ দেন তাই তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণ। এই অভিভাষণের মধ্যে নজরুল ঘোষণা করেন: ‘যদি আর বাঁশী না বাজে-বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসি নি, আমি নেতা হতে আসি নি-আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নিরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।’ নজরুল গবেষক বেগম আকতার কামাল এর মন্তব্য- ‘যে অর্ফিয়ুসের বাঁশিতে তিনি মৃতের বুকে প্রান সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, যে শ্যামের বাঁকা বাঁশের বাঁশরি হয়ে সমাজবন্দি প্রেমকে অভিসারের আকুলতায় মুক্তির পথে টেনে নিতে চাইছিলেন সেই নজরুলীয় বাঁশি না বাজার কৈফিয়ৎকে আমরা কীভাবে নিব?’ গন্ধবিধূর দগ্ধ ধূপের মতোই যিনি নিঃশোষিত হবেন ক্রমশ, ভবিষ্যৎ দ্রস্টার মতো তারই এক ‘সেলফ-পোর্ট্রেট’ আঁকা হয়ে যায় নিচের পঙক্তিগুচ্ছে ঃ ‘তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না / কোলাহল করি’ সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।/ নিশ্চল নিশ্চুপ / আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধূর ধূপ।’ নজরুল গবেষকরা উক্ত পঙক্তিগুচ্ছ সমন্ধে বিশ্লেষণ করবেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যেই নজরুল নিজেও অসুস্থ এবং ক্রমশ নির্বাক ও সম্বিতহারা হয়ে যান। ১৯৪২ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শিশুদের অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের সময় কবি অকস্মাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে যান। উপরোক্ত পঙক্তিগুচ্ছ সত্যে পরিণত হয়-‘কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না। / নিশ্চল নিশ্চুপ’ সৃষ্টি সুখের উল্লাস থেমে গেল। আরম্ভ হয় কবির চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রুষা। শ্যামবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে ডাঃ বিধান রায় কবিকে দেখতে আসতেন এবং তাঁরই নির্দেশে একটা মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। ‘বাবার স্মৃতি’ প্রবন্ধে কবির পুত্র কাজী সব্যসাচী স্মৃতিচারণ করেছেন,- ‘বাবার অসুস্থতার প্রথমদিকে তখন সারা দেশে তার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ। তার মধ্যেই কতলোক যে তাঁকে দেখতে আসতেন, তাঁর আরোগ্য কামনা করতেন। অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যেত। বাবা কাঁপা কাঁপা হাতে কোনো রকমে নিজের নামটা সই করতেন। মাঝে মাঝে দু-এক লাইন কবিতাও লিখতেন- ‘আমি যেমন ভাল ছিলাম/ তেমন ভাল আছি / হৃদয় পদ্মে মধুপেল / মনের মৌমাছি।’
১৯৫২ সালে জুলাই মাসে নজরুল নিরাময় সমিতির উদ্যোগে কবিকে চিকিৎসার জন্য রাঁচি মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১৯৫৩ সালের মে মাসে চিকিৎসার জন্য কবিকে ইউরোপের লন্ডন পাঠানো হয় এবং ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয় ভিয়েনায়। একই বছরে ভিয়েনা থেকে নিরাময় না হওয়ায় ফিরিয়ে আনা হয় কলকাতায়।
১৯৬২ সালে কবি পত্নী প্রমীলার মৃত্যু হয়। কবির নাতনী খিলখিল কাজী ‘হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে’ প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করেছে- ‘কলকাতার ক্রিস্টোফার রোডের দোতলা ফ্লাটে (কবির পরিবার) আড়াইরুমের ফ্লাটে আমরা সবাই কোনোরকমে মাথা গুঁজে থাকতাম। আমি যখন দাদুকে দেখলাম, বুঝতে শিখলাম, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্বাক। একটা খাটের ওপর নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতেন। কখনো বা অনেক খবরের কাগজ পাশে নিয়ে বসে আছেন, কী যেন ভাবতেন আবার পড়ার মত করে বিড়বিড় করে পড়ছেন, তখনি ছিঁড়ে ফেলছেন। সারা ঘরে হাঁটছেন, খোলা জানলার পাশে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে বাবা (কাজী সব্যসাচী) ও চাচা (কাজী অনিরুদ্ধ) ঠিক করলেন, প্রতি মাসে বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করবেন। তাতে দাদুর মনটা ভালো থাকবে, পুরনো দিনের শিল্পী- যাঁরা দাদুর কাছে সঙ্গীতের দীক্ষা নিয়েছিলেন, সবাই এসে কলকাতার সিআইটি ফ্লাটে দাদুকে গানে গানে শ্রদ্ধা জানাতেন। দাদু সেদিন কী যে খুশি হতেন, তা লিখে প্রকাশ করতে পারব না। আঙুর বালা দেবী, ইন্দুবালা, জাস্টিস মাসুদ, ফিরোজা বেগম, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু- আরো অনেক গুণী শিল্পী সেদিন বাড়িতে ভির করতেন, গান করতেন। গানের জলসায় সত্যিই সেদিন নীরব কবি হয়ে বসে থাকতেন দাদু।’ নজরুলের লেখা ‘মৃত তারা’ কবিতার শেষের লাইন মনে করিয়ে দেয়- ‘জ্যোতিহীন বিষহীন ধূমকেতু আজো হায় বেঁচে আছি’:
১৯৭২ সালের ২৪ মে নবগঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি রূপে কবি নজরুল ইসলামকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২৮নং সড়কে একটি বাংলোতে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। ১৯৭৬ সালে ২৮ আগস্ট কবির স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হয়। ২৯ শে আগস্ট (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ ভাদ্র ১২) সকাল ১০.১০ মিনিটে ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গন্ধবিধূর দগ্ধ ধূপের মতোই নিঃশোষিত হলেন। ঐদিন বিকেল সাড়ে চারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে সমাধিস্থ করা হয়।
কবি দারুণভাবে জীবিত আজও। অসহায় মানুষের ক্রন্দনে, অসাম্প্রদায়িক মিছিলের স্লোগানে, প্রেমের মৃদুতম সুরেলা অনুরণনে, শিশুর অনাবিল সরলতার মিতালিতে তিনি এই দেশ ও ভাষায় পুনর্জীবিত হচ্ছেন।
লেখক : সহকারী অধ্যাপক (অবঃ)