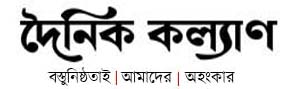নিজস্ব প্রতিবেদক
অবৈধভাবে নদী দখল করে স্থাপনা নির্মাণ, শিল্প কারখানার দূষণ, পলি ভরাটসহ বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত ২২টি নদী সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। ফলে এসব নদী এলাকায় কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, সেচের পানির অপর্যাপ্ততা, জেলেদের জীবিকা হারানোসহ নানা সংকট তৈরি হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, এক সময়ের খরস্রোতা নদীতে এখন যতদূর চোখ যায় শুধু পলি আর পলি। মাত্র দুই বছরের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে সাকো তৈরি করে মানুষ নদী পার হচ্ছেন। খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার এই ভদ্রা নদীর মতো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল তথা খুলনা বিভাগের অন্তত ২২টি নদীর অবস্থা খুবই সংকাটাপন্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি এক জরিপে এসব নদীর তালিকা প্রণয়ন করা হয়।
এর মধ্যে খুলনার ময়ূর, ভৈরব, শোলমারি, হামকুড়া, কাজীবাছা, যশোরের হরিহর, টেকা, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ার কুমার, কালিগঙ্গা, বাগেরহাটের ভোলা, চুয়াডাঙ্গার নবগঙ্গা, ঝিনাইদহের বেতনা সাতক্ষীরার ইছামতী নদী অন্যতম। মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে আরও অনেক নদী।
অভিযোগ রয়েছে, বছরের পর বছর এসব নদী পাড়ে অবৈধ দখল করে স্থাপনা নির্মাণ, শিল্প কারখানার দূষণ নদী মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলেও তা উচ্ছেদে ব্যবস্থা নেয়া হয় না। সেই সঙ্গে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ, সেতু ও স্লুইচগেট নির্মাণ, খালের সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও পলির অব্যবস্থাপনার কারণে নদীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে।
পানি উন্নয়ন বোর্ড আর বিআইডব্লিউটিএ অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য তালিকা হলেও অজানা কারণে তা আর হয় না। কোথাও কোথাও ড্রেজিং করা হলেও বছর ঘুরতেই আবারও নদী ভরাট হয়ে যায়। ফলে এসব অঞ্চলের কৃষি জমিতে তৈরি হচ্ছে জলাবদ্ধতা, বাড়ছে লবণাক্ততা, ফসল চাষের জন্য কৃষকরা পাচ্ছেন না পর্যাপ্ত সেচের পানি, জেলেরা হয়ে পড়ছেন কর্মহীন। ফলে নদীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবিকা নির্বাহ বছরের পর বছর দুঃসহ হয়ে উঠছে।
বটিয়াঘাটা উপজেলার সুরখালি ইউনিয়নের জেলে আব্দুর রহীম বলেন, এই নদীতে এক সময় ৮০/৯০ হাত পানি থাকতো। এখন হেঁটে পার হই আমরা। এই নদীই ছিলো আমার আয়ের উৎস। বাবার পর আমি এই নদী থেকে মাছ ধরে সংসার চালাতাম। কিন্তু এই নদী থেকে এখন আমি বা আমাদের এই এলাকার কোনো জেলে পরিবার কিছুই করতে পারি না। আমাদের সংসারই চলে না। অন্য কাজও তো করতে পারি না। নদী না কাটলে আমাদের আর কিছুই করার থাকবে না।
একই ইউনিয়নের আরেক বাসিন্দা মোল্লা খবির আহমেদ বলেন, নদীতে পানি না থাকায় জমিতে সেচের পানি দিতে পারি না। এ বছর ফসল ফলেছে অর্ধেকেরও কম। আর বৃষ্টির সময় তো পুরো এলাকায় পানি জমে থাকে। জলাবদ্ধতায় ফসল হয় না। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী বছর হয়তো আমরা কোনো ফসলই ফলাতে পারবো না।
এ দিকে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় দুই পাড়ের মানুষের পারাপারেও নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলাকাবাসী নিজেরা নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করেছেন। ওই বাঁশের সাকো পার হচ্ছিলেন প্রায় সত্তর বছর বয়সী নিমাই চন্দ্র। তিনি বলেন, বয়সের ভারে চলাই কষ্ট। এখন বাঁশের সাঁকো পার হওয়া তো আমাদের জন্য আরও কষ্টকর।
এসব নদী বাঁচাতে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন বছরের পর বছর আন্দোলন করে আসছে। করছে নানা সুপারিশও। কিন্তু কোনো সুপারিশেই খুব একটা কাজে আসছে না বলে জানান বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মাহফুজুর রহমান মুকুল।
তিনি বলেন, নদীর কারণেই কিন্তু জনপদ সৃষ্টি হয়েছে। নদী না থাকলে কোনো কিছুই থাকবে না। আমরাও থাকবো না। আমরা বারবার বিভিন্ন ফোরামে একথা বলে আসছি। উচ্চ আদালতের একাধিক নির্দেশনা থাকলেও তাও কার্যকর হচ্ছে না। নদীরক্ষায় আমাদের সুপারিশ হচ্ছে, পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টিকারী সব অবৈধ বাঁধ অপসারণ, সব চর দখলমুক্ত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ বিধিমালা ১৯৯৭ বিবেচনায় নিয়ে নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করা, ১৯৯৫ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নদী-খাল ইজারা বন্ধ করা, পর্যায়ক্রমে নদীর সব ধরনের বাধা অপসারণ, হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী নদের সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা এবং নদীর সঠিক সীমানা নির্ধারণ করে সীমানা সুরক্ষা ইত্যাদি।
এ দিকে এ নিয়ে খুলনা নদী বন্দর কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, নৌপথ ঠিক করার জন্য নদীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমাদের তালিকা আছে। নদী পাড়ে অবৈধ দখলদারের তালিকাও আছে। নদীতে ড্রেজিংয়ের জন্য আমাদের পরিকল্পনা আমরা ড্রেজিং বিভাগে পাঠিয়েছি। শিগগিরই নদীগুলো ড্রেজিংয়ের আওতায় আনা হবে। আর অবৈধ দখলদারের তালিকা আমরা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে পাঠিয়েছি। যে কোনো সময় উচ্ছেদ করা হবে।
এ নিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মো. আশরাফুল আলম বলেন, আমাদের এখন টেকসই ড্রেজিং দরকার। এ জন্য আরও ভালো স্টাডি প্রয়োজন। আমাদের স্টাডি শেষে নদী সিস্টেম নিয়ে প্রকল্প আকারে প্লানিং কমিশনে পাঠাবো। আশা করি দ্রুতই নদী বাঁচাতে কাজ শুরু হবে।
খুলনা বিভাগে মোট ৮৭টি নদীর মধ্যে ৫২টি স্থানীয়, ৫টি আঞ্চলিক, তালিকাবিহীন নদী রয়েছে ২২টি।