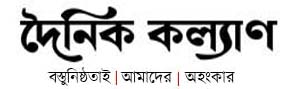“অন্যদিকে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টিও প্রকাশ করা হচ্ছে। তার মতো অসংখ্য একা মানুষ আমাদের সমাজে আছে, তাদের হতাশা বাড়ানোর জন্য এই তথ্যটিও কি কাজ করবে না? পত্রিকাগুলো যখন প্রথম পৃষ্ঠায় লক্ষণীয় স্থানে এই আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ করে, তখনও কি এমন মানুষগুলোর হতাশা বাড়বে না? অথচ এমন অসহনীয় সংবাদটি কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জায়গা পেলেই ভালো হতো”
মোস্তফা হোসেইন: সম্প্রতি একজন সেলিব্রিটির শ্বশুরের আত্মহত্যার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে মূলধারার গণমাধ্যমে আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনার ঝড় বইছে। সংবাদ থেকে শুরু করে মন্তব্য সবখানেই ক্ষোভ লক্ষণীয়। কিন্তু ক্ষোভটা কার বিরুদ্ধে? অনেকেই বলছেন, সামাজিক অবক্ষয়ের কথা। বলছেন, মানুষ যখন মেশিনের মতো হয়ে যায়, মানুষ যখন শুধু ঊর্ধ্বমুখী চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন এমন প্রতিক্রিয়াই তৈরি হয়। যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে। আর আত্মহত্যায় উসকে দেওয়ার কথাও অনেকে বলছেন।
বৈজ্ঞানিকভাবেও এসব ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার চেষ্টা কি আছে? এই যে উসকে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাকে নিবৃত করার কোনো উদ্যোগও কি আছে? আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে বলতে হবে, রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক কোনোভাবেই উদ্যোগ নেই। নেই ব্যক্তিগত কোনো উদ্যোগও।
উসকে দেওয়ার মতো উপকরণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিকটজনের আচরণ। গণমাধ্যমও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে কমবেশি। সাম্প্রতিক ঘটনাটির সূত্রে গণমাধ্যমে যেসব সংবাদ ও মন্তব্য প্রচার হয়েছে, তার প্রায় প্রতিটিতেই উসকে দেওয়ার মতো উপাদান আছে। সেলিব্রিটির শ্বশুর আত্মহত্যা করেছেন, এখানে সেলিব্রিটির ভূমিকাটা কী? অথচ তার নাম পরিচিতি উল্লেখ করাটাই গণমাধ্যমের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হয়েছে স্পষ্ট। দর্শক এবং পাঠক সংবাদগুলোতে আত্মহননকারীর চেয়ে সেলিব্রিটির পরিচয়কেই বেশি দেখছে। এই প্রবণতাকে কি উসকে দেওয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হলে ভুল হবে?
অন্যদিকে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টিও প্রকাশ করা হচ্ছে। তার মতো অসংখ্য একা মানুষ আমাদের সমাজে আছে, তাদের হতাশা বাড়ানোর জন্য এই তথ্যটিও কি কাজ করবে না? পত্রিকাগুলো যখন প্রথম পৃষ্ঠায় লক্ষণীয় স্থানে এই আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ করে, তখনও কি এমন মানুষগুলোর হতাশা বাড়বে না? অথচ এমন অসহনীয় সংবাদটি কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জায়গা পেলেই ভালো হতো।
গণমাধ্যমগুলোতে পরিত্রাণের উপায়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের প্রচার-প্রকাশে সে দিকটি কার্যত উপেক্ষিত থাকছে। সামাজিক পরিবর্তনের এই ব্যাধি থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে কিছু বলছে না।
অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মহামারি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে যেভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, সামাজিক অবক্ষয় রোধজনিত জীবনহানি রোধ করতে তার উল্টো চিত্রই চোখে পড়ে। আমরা দেখেছি, করোনায় মৃত্যুর মতোই এই মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করার মতো পর্যায়ে চলে গিয়েছে। করোনার কারণেও মানুষের বিষণ্নতা বাড়ছে, অর্থাৎ আত্মহত্যার একটি কারণ হিসেবে করোনাকেও দায়ী করা যায়। সে ক্ষেত্রে করোনায় মৃত্যুর মতো এই আত্মহত্যায় মৃত্যুকেও গুরুত্বসহ বিবেচনা করা উচিত।
আত্মহত্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে উন্নত দেশগুলোতে মন্ত্রী নিয়োগ এবং গবেষণায় জোর দেওয়ার উদাহরণ আমরা পাই। এই তো, ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্য সরকার সেখানকার মানুষের মন থেকে বিষণ্নতা দূর করতে তথা নিঃসঙ্গতা দূর করায় উদ্যোগী হয়ে মন্ত্রী নিয়োগ করেছিল। গত বছর করোনার কারণে মানুষের নিঃসঙ্গতা বেড়ে যাওয়ায় জাপানের সরকার সেখানে একজন মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন মানুষকে এই ব্যাধি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে করণীয় কীÑনির্ধারণের জন্য।
যুক্তরাজ্য কিংবা জাপানের মতো দেশে যখন আত্মহত্যার কারণে দেশের সরকার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয় এবং আত্মহত্যার কারণগুলো নিরসনের জন্য মন্ত্রী পর্যন্ত নিয়োগ করে, তখন বুঝতে হবে দারিদ্র্যই আত্মহত্যার মূল কারণ নয়। গবেষণায়ও এর জবাব পাওয়া যায়, দেশ-কালভেদে এই আত্মহত্যার কারণগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে। তার মানে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোর আত্মহত্যার কারণ হিসেবে দারিদ্র্য থাকলেও বৈশ্বিক কারণ হিসেবে দারিদ্র্য একমাত্র কিংবা প্রধান কারণ নয়। কিন্তু এটা ঠিক, বিভিন্ন কারণে মানুষ যখন নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবতে শুরু করে, বিষণ্নতা যখন তাকে আক্রান্ত করে, তখন আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটায়।
আবার বাংলাদেশে সম্প্রতি এক সেলিব্রিটির শ্বশুর আত্মহত্যা করলেন, তিনি কি দরিদ্রতার কারণে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করেছেন?
আত্মহত্যার কারণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। নিঃসঙ্গতা থেকে তৈরি বিষণ্নতাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয় আত্মহত্যার জন্য। আর এই নিঃসঙ্গতাই যে সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যাটির পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তা-ও আলোচনায় বেরিয়ে এসেছে। তাহলে এই নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য করণীয় কী?
বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। পরিবারের বৃদ্ধরা একাকী হয়ে যাচ্ছেন।কিশোর-তরুণরা অধিকতর প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় তাদের সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। করোনাকালে অনলাইন ক্লাস, অনলাইন অফিসনির্ভরতা বৃদ্ধির কারণে তৈরি হয়েছে নতুন মাত্রার নিঃসঙ্গতা। কর্মসূত্রে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সন্তান, একাকী হয়ে পড়ছে বাবা-মা। অধিক প্রযুক্তিনির্ভরতা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করছে ব্যাপকভাবে।
বৈশ্বিক মহামারি করোনায় মানুষকে নিঃসঙ্গ থাকার প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে। পরিণতিটা কী দাঁড়িয়েছে? গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আঁচল নামের একটি সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ওই সময় করোনায় মারা গিয়েছে পাঁচ হাজার মানুষ আর আত্মহত্যা করেছে প্রায় ১১ হাজার মানুষ। বাংলাদেশে গত বছর এই সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে জাপানের একটি পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে, তাদের ওখানে ১০ বছরের মধ্যে অন্তত ২০ গুণ আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েছে। যে কারণে সরকারকেও উদ্যোগ নিতে হয়েছে আত্মহত্যার কারণগুলো দূর করার বিষয়ে।
প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকারিভাবে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে, মানুষও এর উপকারিতা দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কিন্তু এর যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে, সেদিকে কারও নজর নেই। যে কারণে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে জীবনব্যবস্থায়। একসময় বাবা-মা-সন্তান পরিবারে থাকার পর প্রয়োজনীয় কিংবা বিনোদনমূলক আলোচনা করতেন। হালে বাবা-মা ও সন্তান একই ঘরে থাকার পরও তাদের দূরত্ব কমছে না। কারণ, সন্তান ঘরে ঢুকেই মোবাইল কিংবা ল্যাপটপ হাতে নিয়ে বসে। প্রযুক্তিনির্ভরতার মাত্রা নির্ধারণ বিষয়ে এখন ভাবার সময় এসে গেছে।
যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে হালে। স্বাভাবিক কারণেই পরিবারের বৃদ্ধ মানুষগুলো একাকী হয়ে পড়ছে। যৌথ পরিবার পদ্ধতি টিকিয়ে রাখা এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু একটি পরিবার থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার সৃষ্টি হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের যে দূরত্ব তৈরি হয়, সেই দূরত্ব কমিয়ে আনার ব্যাপারে কৌশল নির্ধারণ করা এই মুহূর্তে জরুরি।সমাজবিজ্ঞানীদের ভূমিকা আছে এখানে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়ে গবেষণা কতটা হয়, জানা নেই। কিংবা তাদের গবেষণার ফল কতটা কার্যকর হয়, তা-ও অজানা।
একজন ব্যবসায়ী আত্মহনন করেছেন, প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী তার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে, সেই কারণগুলো আমাদের সমাজে ব্যাপক। এই প্রবণতার লাগাম টানতে হলে সেসব কারণ থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি বলে মনে করি।
লেখক : সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক