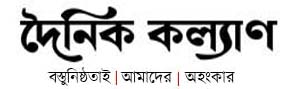“প্রমিত ভাষায় কথোপকথনের ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনেও দেখা যাচ্ছে চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। বিগত শতকের ষাট, সত্তর ও আশির দশকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অহংকারের জায়গা ছিল প্রমিত ভাষায় কথোপকথনের সামর্থ, দক্ষতা ও চর্চা। কিন্তু সে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন থেকে প্রমিত ভাষা খুবই দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সমাজবিজ্ঞানের পাঠ ও আধ্যয়নিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী মধ্যবিত্তের সামাজিক শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণে ভাষার এ লৈখিক ও বাচনিক দক্ষতাও একটি অন্যতম মানদণ্ড বৈকি! ফলে বাংলাদেশের সমাজ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে যে উদ্বেগ ক্রমশই জোরদার হচ্ছে, তার পেছনে উল্লিখিত শ্রেণির ভাষিক দক্ষতা হারানোর দায়ও নেহায়েত কম নয়।”
আবু তাহের খান
এই সেদিন পর্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের শুরুতে পরীক্ষার্থীদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হতো যে, ‘সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দোষণীয়’। শিক্ষার্থী যাতে তার লিখন ও পঠনে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রে মান ও শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে তজ্জন্যই ছিল এ প্রয়াস, যে চেষ্টা ভুল ছিল না মোটেও।
আর ভুল যে ছিল না তার প্রমাণ এই যে, ঐসব বর্ণনামূলক প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর স্তর মূল্যায়নের রীতি যতদিন চালু ছিল, ততদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা একটি ন্যূনতম মান নিয়ে বেরুতেন বলেই এখন ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছে। এবং এটিও মনে করা হচ্ছে যে, এ বর্ণনামূলক পরীক্ষারীতি বিসর্জন দেওয়ার ফলেই শিক্ষার গুণগত মান দিন দিন পড়ে যাচ্ছে (অবশ্য মান পড়ে যাওয়ার অন্যবিধ কারণও রয়েছে)। অধিকন্তু বর্ণনামূলক প্রশ্নরীতি বিসর্জন দিয়ে যখন থেকে ‘সত্য-মিথ্যা’র বহুনির্বাচনী পরীক্ষারীতি চালু করা হলো, তখন থেকে হারাতে বসল শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞানের মান এবং সেইসঙ্গে তার শুদ্ধ ভাষাচর্চ্চার সামর্থও। আর তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক সনদধারী তরুণই এখন প্রমিত মানের শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পারেন না, এমনকি তা পারেন না বহুনির্বাচনী পরীক্ষাপদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হয়ে আসা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বহু শিক্ষকও।
উপরোক্ত বিষয়গুলোকে উদাহরণের আলোকে যাচাই করা যাক। শিক্ষার্থী যে প্রমিত মান রক্ষা করে লিখতে, পড়তে বা বলতে পারেন না, তার সবচেয়ে বড় ও প্রথম সাক্ষী হচ্ছেন তার শিক্ষকগণ। তবে সনদলাভের পর কাজ খুঁজতে গিয়ে কর্মদাতার সামনেও অহরহ তাকে সে অক্ষমতার মুখে পড়তে হয় বৈকি এবং সে ক্ষেত্রে তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসে ভাষা ও জ্ঞান উভয়বিধ অজ্ঞানতার ফিরিস্তিসমূহ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে শিক্ষার্থীদের নানা লেখাজোখা ও কথাবার্তায় তাদের এ মানের বিষয়টি এখন হরহামেশা এবং অতি সহজেই চোখে পড়ছে।
তবে এতো গেল শিক্ষার্থীদের কথা, যারা এখন সবে শিখছেন। কিন্তু তাদের যারা শেখাচ্ছেন, প্রমিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের কী হালহকিকত! দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বহুনির্বাচনী পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হয়ে আসা শিক্ষকগণের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ, যা উপরে উল্লেখ করা হলো।
ফেসবুকে তাদের অনেকের লেখালখির মান ও স্তর দেখলে রীতিমতো ভিরমি খেতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যায়ের সম্মানিত শিক্ষকদের কারো কারো লেখায়ও দেখি কষ্টদায়ক ভুল ভাষা, বাক্য ও বানানের অজস্র ছড়াছড়ি। আর জনসমক্ষে যারা এ মানের ভাষা ব্যবহার করেন, সাধারণের চোখের আড়ালে শ্রেণিকক্ষে তারা কী করেন, সেটি কেবল তারা ও তাদের শিক্ষার্থীরাই ভালো বলতে পারবেন। তা প্রমিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অংশগ্রহণের মান ও স্তর যদি এই হয়, তাহলে কীভাবে আশা করা যাবে যে, সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক পথ ধরে এগুচ্ছে? তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে নানাবিধ সমালোচনা চালু থাকার পরও সেসবকে ধন্যবাদ এ কারণে যে, এর কল্যাণেই আমাদের শিক্ষকদের একটি অংশের মান ও স্তর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।
বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে বর্তমানে যেসব অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হয়, সেসবের সিংহভাগ অংশগ্রহণকারীই কথা বলেন বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে অশুদ্ধ ভাষায়। এমনকি মধ্যরাতের যেসব অনুষ্ঠানে শিক্ষিত সুধীজনরা অংশ নিচ্ছেন, তাদের মুখেও শুনি বাংলা-ইংরেজির অপ্রয়োজনীয় দূষণীয় মিশ্রিত ভাষা। আর সাধারণ পাত্রপাত্রীতো নিজেদের অনেকটা চৌকস প্রমাণ করার জন্যই অপ্রয়োজনে ইংরেজি বলে থাকেন। কিন্তু তারা মোটেও বুঝেন না যে, এতে তারা চৌকস প্রমাণিত হওয়ার পরিবর্তে উপহাসের পাত্র হচ্ছেন। তবে তারা যে অশুদ্ধ-অপ্রমিত ভাষায় কথা বলছেন, তজ্জন্য তাদের মোটেও দোষ দেওয়া যাবে না।
কারণ তারা যে যতটুকু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই গ্রহণ করে থাকুন না কেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাকে সে স্তরের ভিত্তি পর্যায়ের ভাষাজ্ঞানটুকুই দেয়নি। কিন্তু মধ্যরাতের অনুষ্ঠানে যে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা অংশ নিচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে অপ্রমিত ভাষার ও বাংলা-ইংরেজির মিশ্রণযুক্ত কথোপকথন কোনোভাবেই কাম্য নয়। সবচেয়ে হতাশার কথা, ভাষা ও সাহিত্যের নানা শাখায় ও পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্তৃক যাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, তাদের ভাষা, বাক্য ও বানানেও দেখি অজস্র ভুল এবং অপ্রমিত ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার। দেখে ঠিক বুঝে ওঠা যায়না, এটি পুরস্কারদানের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ত্রুটি নাকি শিক্ষার সামগ্রিক মানেরই অধঃগামিতা!
প্রমিত ভাষায় কথোপকথনের ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনেও দেখা যাচ্ছে চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। বিগত শতকের ষাট, সত্তর ও আশির দশকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের অহংকারের জায়গা ছিল প্রমিত ভাষায় কথোপকথনের সামর্থ, দক্ষতা ও চর্চা। কিন্তু সে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন থেকে প্রমিত ভাষা খুবই দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, সমাজবিজ্ঞানের পাঠ ও আধ্যয়নিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী মধ্যবিত্তের সামাজিক শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণে ভাষার এ লৈখিক ও বাচনিক দক্ষতাও একটি অন্যতম মানদণ্ড বৈকি! ফলে বাংলাদেশের সমাজ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে যে উদ্বেগ ক্রমশই জোরদার হচ্ছে, তার পেছনে উল্লিখিত শ্রেণির ভাষিক দক্ষতা হারানোর দায়ও নেহায়েত কম নয়।
একই অবস্থা সরকারি দফতরেও। সেখানেও বাংলা ভাষার প্রমিত ব্যবহার-পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে যেমনি অভিধান বহির্ভূত শব্দ ‘প্যারা’ ব্যবহৃত হচ্ছে ‘সমস্যা’র প্রতিশব্দ হিসেবে কিংবা অবলীলায় ইংরেজি শব্দ বা বাক্য ঢুকে যাচ্ছে এরচেয়ে উঁচু মানের সমান্তরাল বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও তেমনি অবস্থা সরকারি দফতরেও। স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি খুঁজতে গিয়ে প্রথম বাক্যটিই পাওয়া গেল ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’ শিরোনামে। বাংলা ভাষার প্রতি কি আশ্চর্যজনক অবহেলা নাকি উপহাসমূলক অবজ্ঞা! ‘মাস্ক ছাড়া সেবা নয়’-কোন অর্থে ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’-এর চেয়ে অধঃমানের? কিন্তু সেটি না করে করোনার ঝুঁকিতে থাকা ১৭ কোটি মানুষকে তারা এভাবেই অপ্রয়োজনে নিরন্তর নানা ইংরেজি শব্দ শিখিয়ে যাচ্ছে। তাদের ওয়েবসাইটের বাংলা বানান-বাক্যেও দেখছি অসংখ্য ত্রুটি। আর এটি শুধু স্বাস্থ্য অধিদফতরের ক্ষেত্রেই নয়-অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা, একই হালে চলছে তাদের দাফতরিক ভাষাচর্চাও। এটি তাদের অদক্ষতার জন্য যেমনি ঘটছে, তেমনি ঘটছে ভাষার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা থেকেও।
অভিযোগ আছে যে, মানুষ এখন পড়তে চায় না, বরং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা টেলিভিশনে দেখে বা শুনে পড়ার কাজটি সেরে ফেলতে চায়। সে ক্ষেত্রে টেলিভিশন তাদের অনেকখানি সহায়তা করে। অর্থাৎ টেলিভিশনের ওপর মানুষের নির্ভরতা এখন অনেকখানি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সংবাদে, স্ক্রলে ইত্যাদি প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই ইংরেজি শব্দের মিশ্রণমুক্ত প্রমিত বাংলার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে টেলিভিশনের মাধ্যমে ভাষার এ অপ্রমিত ব্যবহার-প্রবণতার সাথে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এর নেতিবাচক প্রভাব দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে। কিন্তু বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহল আদৌ গুরুত্বের সাথে অবলোকন করছেন বলে মনে হয় না। তাদের এ ধরনের দায়িত্বহীন আচরণ বাংলা ভাষার মানসম্মত চর্চা ও বিকাশের ধারাকে বস্তুতই অনেকখানি পিছিয়ে দিচ্ছে।
ভাষার জন্য রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে শুরু হওয়া যে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত এ দেশকে স্বাধীনতা এনে দিল, সেই সংগ্রামের ফল হিসেবে আজ যদি এটিই দেখতে হয় যে, ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আমরা গত শতকের ষাট, সত্তর বা আশির দশকের চেয়েও পিছিয়ে পড়েছি, তাহলে একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে অহংকার করার জায়গাটি বস্তুতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় না কি? এটি কি ভাবা যায়, এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি এখন ইংরেজির মিশ্রণবিহীন প্রমিত বাংলায় কথা বলতে, বক্তৃতা করতে, আলোচনায় অংশ নিতে বা দৈনন্দিন কথোপকথনে অপারগ বা অনভ্যস্ত? সবাই না হোক, অন্তত ভাষাচর্চার বিদ্যমান বেহাল অবস্থা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধঃগামী ক্ষয়িষ্ণুতা দেখে মনে মনে কষ্ট পান, তারা অন্তত মাতৃভাষাকে এ চরম দুর্যোগ থেকে পুনরুদ্ধারে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা রাখি।
লেখক : গবেষক ও প্রাবন্ধিক ধঃশযধহ৫৬@মসধরষ.পড়স