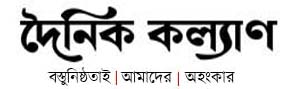জীবনের পড়ন্ত বেলায় আশার ছলনায় ভুলে মাইকেল কী ফল লাভ করেছিলেন? কিন্তু সারা জীবন তাঁর প্রত্যাশা এক ছিলো না। তরুণ বয়সে তাঁর অগ্রাধিকার ছিল কবি হয়ে যশ লাভ করার, এমন কি, নীল নয়নার প্রেম লাভ করার। তবে অর্থস্বাচ্ছন্দ্য এবং আদরের মধ্যে মানুষ হন বলে সেই তরুণ বয়স থেকে বস্তুগত ভোগ এবং সুখের প্রতিও তাঁর লোভ কিছু কম ছিলো না। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির অসঙ্গতিও দেখা দিতে আরম্ভ করে সেই হিন্দু কলেজের আমল থেকে। বিয়েকে কেন্দ্র করে বাবা মা’র সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য থেকে তাঁর হতাশার সূচনা। আর কাঙ্খিত ভোগ-সুখে ঘাটতি পড়েছিলো বিপশপস কলেজ ত্যাগ করার আগে থেকেই। কিন্তু সাহিত্যিক হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের
জীবনের পড়ন্ত বেলায় আশার ছলনায় ভুলে মাইকেল কী ফল লাভ করেছিলেন? কিন্তু সারা জীবন তাঁর প্রত্যাশা এক ছিলো না। তরুণ বয়সে তাঁর অগ্রাধিকার ছিল কবি হয়ে যশ লাভ করার, এমন কি, নীল নয়নার প্রেম লাভ করার। তবে অর্থস্বাচ্ছন্দ্য এবং আদরের মধ্যে মানুষ হন বলে সেই তরুণ বয়স থেকে বস্তুগত ভোগ এবং সুখের প্রতিও তাঁর লোভ কিছু কম ছিলো না। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির অসঙ্গতিও দেখা দিতে আরম্ভ করে সেই হিন্দু কলেজের আমল থেকে। বিয়েকে কেন্দ্র করে বাবা মা’র সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য থেকে তাঁর হতাশার সূচনা। আর কাঙ্খিত ভোগ-সুখে ঘাটতি পড়েছিলো বিপশপস কলেজ ত্যাগ করার আগে থেকেই। কিন্তু সাহিত্যিক হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের
সাজেদ রহমান
আসরে স্থান পাওয়ার স্বপ্ন তখনও ভেঙ্গে যায়নি। সেই আঘাতটা এসেছিল ক্যাপটিভ লেডি প্রকাশের
পর। তবে তখনও হতাশা এসেছিল সাময়িকভাবে। কলকাতায় এসে বাংলা সাহিত্যের দরবারে রাতারাতি একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি এবং নাট্যকার বলে স্বীকৃতি লাভের পর আগেকার হতাশা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগেনি। অতঃপর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কবি নিজেকে কখনও কখনও কালিদাস, ভার্জিল, এমন কি মিল্টনের সমকক্ষ বলেও মনে করেছেন।
বস্তুত, যতদিন যশের তুঙ্গে উঠতে পারেননি, যতদিন তাঁর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, ততদিন তিনি গুরুত্বের সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। কিন্তু মাত্র চার বছরের মধ্যে যখন তাঁর সামনে আর কোনও সাহিত্যিক লক্ষ্য থাকলো না, যা কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, তার সবই সহজে অর্জন করলেন, তখন তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেলেন। বিশপস কলেজের অন্যতম অধ্যাপক তরুণ মাইকেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, মিশনারি হবার আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে কত প্রবল, বস্তুগত ভোগের লোভে তিনি সেটা বুঝতে পারছেন না। একই রকম বলা যায় যে, সাহিত্য রচনা করে কেবল যশ লাভ করা নয়, সাহিত্যের প্রতি তাঁর সত্যিকার প্যাশন কত জোরালো, ধনী হবার লোভে তিনি তারও পরিমাপ করতে পারেননি। নয়তো ব্যারিস্টারি পড়ার কথা তিনি ভাবতেন না। এমন কি, সোনার হরিণের লোভে তিনি যখন ব্যারিস্টার হয়েছেন, তখনও আদালতের মতো অ-কাব্যিক স্থানেও তিনি বারবার আইনের বদলে তাঁর সহজাত প্রেম যে সাহিত্যের প্রতি তা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত, তিনি কেবল কবি নন, তিনি মনেপ্রাণে কবি।
একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন: যার ভাগ্য-সরোবরে মা কমলা সোনালি আলোতে কমলিনী-রূপে বিরাজ করেন না, এ পৃথিবীতে তার জন্ম কুক্ষণে হয়েছে-এমনটা মনে করার কারণ নেই। কারণ, কল্পনারূপ খনির মধ্য থেকে রত্ন কুড়িয়ে এনে নিজের ভাষাকে যে সাজায় এবং ভাষার অঙ্গ-শোভা বৃদ্ধি করে, তার ধন কেউ কেড়ে নিতে পারে না, সে অমরত্ব লাভ করে। তিনি ‘বড়ো লোকে’র মত জীবনযাপন করতে চেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা ছিলো; তিনি মানুষের মাঝখানে অমর হয়ে থাকবেন। যা লিখেছেন, তা দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন কিনা, সে চিন্তা তাই তাঁকে বারবার ভাবিত করেছে। তাই লিখেছেন-লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে/বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?/ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,/মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?/অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,/ ঘুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,-/ নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,/ বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে?-
মনের মধ্যে সন্দেহ উঁকি দিলেও কবি আশা করেছেন, উত্তর-কাল তাঁকে মনে রাখবে। অন্তত, তিনি সেই প্রার্থনাই জানিয়েছেন-‘রেখো, মা, দাসেরে মনে। বিলাসী জীবনযাপনের সাধনায় যদি প্রমাদ ঘটে, তবু তোমার মনের লাল পদ্মটিকে মধুহীন কোরো না।’ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি প্রমাদ ঘটিয়েছেন, বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে লেখা তাঁর এই কবিতায় তিনি নিজেই সে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে কত বড় ভুল করেছিলেন এবং পরে আরও বহু ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে সে ভুলকে কত বিশাল করে তুলেছিলেন-সেটা একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় না। এই প্রমাদের জন্যে এবং তিনি যে-এক সময়ে ভিন ধর্ম গ্রহণ করে প্রমাদ ঘটিয়েছিলেন, তার জন্যে বঙ্গ সমাজও সাময়িকভাবে তাঁর প্রতি কম অবহেলা দেখায়নি। যে-অযত্নের মধ্যে তিনি মারা যান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা কমই আছে। মারা যাবার পর, বঙ্গসমাজ তাঁর প্রতি যে- অবজ্ঞা এবং উদাসীনতা দেখায়, সে-ও বিরল। জীবদ্দশায় অথবা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোন কোন কবি কাঙ্খিত যশ লাভে ব্যর্থ হন সে সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিদের সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সুবিদিত। এ কবিতা লেখার সময়ে তাঁর নিজের ভাগ্যের কথাও তিনি ভেবে থাকবেন।
ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,/জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।/উরুপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা/ওমর (অসংখ্য কালে জন্ম তাঁর) যথা অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল/ মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে/ গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে/ বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল/ এ নগর ও নগরে, ‘আমার উদরে/ জনম গ্রহিয়াছিল ওমর সুমতি।’
কবি হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তকে গভীর শ্রদ্ধা করার কোন কারণ দেখেননি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। ঈশ্বর গুপ্ত যে-জগতে বাস করতেন আর তাঁর জগৎ-এ দুই ছিলো একবারে আলাদা। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর গুপ্ত মারা যাবার পরে তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে বাঙালিরা যে কিছুই করেননি, সে কথা বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। দেশের প্রতি হরিশ মুখার্জির অবদানের কথা চিন্তা করে তাঁর অকাল মৃত্যুর পর কবি তাঁর একটি স্ট্যাচু নির্মাণের জন্যে ওকালতি করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা মনে রেখে বলকাতার লোকেরা যখন শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তখনও তিনি তার জন্যে এক মাসের বেতন চাঁদা হিসেবে দিতে তৈরি ছিলেন। যিনি এভাবে অন্যের কীর্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে উদগ্রীব ছিলেন, সেই কবির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কবরের ওপর একটি মানানসই স্মৃতিসৌধ তৈরি করার ব্যাপারে সাহিত্যামোদীরা তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও উদ্যোগ নেননি। অথচ সে সময়ে বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষিত এবং ধনী লোকদের অভাব ছিল না। শ্রাদ্ধতে লাখ টাকা ব্যয় করা, অথবা লাখ টাকা দিয়ে রক্ষিতা রাখার ঘটনা ওই শতাব্দীতেই ঘটেছিলে। তাঁর মৃত্যুর বারো-চোদ্দো বছর পরে যাঁরা তাঁর স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ বাংলা সাহিত্যোকাশের গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ছিলেন না। তাঁদের এ উদ্যোগ নেবার কারণ কবির সঙ্গে তাঁদের এক কালের বন্ধুত্ব। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা যে একেবারে কম ছিল, তাও নয়। তবে সব বন্ধুই তাঁর স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে এক রকমের ধারণা পোষণ করতেন না। যে-বিদ্যাসাগর-কবির ভাষায় তাঁকে ‘নিজ হাতে টেনে তুলেছিলেন’ বিপদের সাগর থেকে, এক জীবনীকারের মতে, সেই বিদ্যাসাগরের কাছে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্যে যখন চাঁদা চাওয়া হয়, তখন তিনি তা দেননি। তিনি নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন, যাঁকে জীবদ্দশায় রক্ষা করতে পারেননি, তাঁর স্মৃতিসৌধ তৈরিতে কিছু দেওয়া অর্থহীন।
মাইকেল খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং স্বসমাজ ত্যাগ করে ইংরেজ সাজতে চেষ্টা করেছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে ঘর করেছিলেন-আপাতদষ্টিতে মনে হয়-তাঁর এই ‘অপরাধে’র কারণে বাঙালিরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি হারিয়েছিলেন। নয়তো, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে তিনি যে-অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন, তাতে তাঁকে নিয়ে বাঙালিরা অনেক বেশি গর্ব করতে পারতেন। তা ছাড়া, তাঁর অ-গতানুগতিক আচরণ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাঁরা আর-একটু বেশি দরদী এবং শ্রদ্ধাশীলও হতে পারতেন। বিশেষ করে তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাঙালিরা তাঁর প্রতি সমুচিত সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কবি হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন, সেটা তাঁর সমকালীন সাহিত্য-রসিকদের বুঝতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশক পরে ধীরে ধীরে ব্যক্তি মাইকেলের প্রতি বিতৃষ্ণা যখন কমে এসেছে, তখন কেউ কেউ তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন। সে ক্ষেত্রেও অবশ্য তিনি যে-অন্তরের অন্তস্থলে হিন্দু ছিলেন-এটাকে বড় করে দেখানোর প্রয়াস একেবারে দেখা যায় না, তা নয়। অর্থাৎ সেখানেও সাহিত্যের চেয়ে তিনি ‘আমাদের লোক’ এই চিন্তাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
বস্তুত, মাইকেলের প্রতি সেকালের বাঙালি সমাজের মনোভাব ছিল একই সঙ্গে ভালোবাসা এবং ঘৃণার। সে জন্যে তাঁকে এক হাতে দূরে সরিয়ে রাখলেও, বাঙালি সমাজ তাঁকে ভুলেও যেতে পারেনি। বরং সময়ের দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি বাঙালিদের শ্রদ্ধা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁর অনুকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে যুগের এবং জীবনধারার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তা ছাড়া, পুরাণের জগৎও প্রাত্যহিক জগৎ থেকে আরও দূরে সরে গেছে। তদুপরি, দেশ বিভাগের পর, হিন্দু পুরাণের সঙ্গে বাঙালি সমাজের একাংশের অপরিচয়ও গভীর হয়েছে। ভাষার ব্যাপক পরিবর্তনও হয়েছে। তা সত্ত্বেও, মধুসূদন-রচিত সাহিত্যে সময়ের ছাপ পড়েছে বলে মনে হয় না। আজকের পাঠকের কাছে সে সাহিত্য আদৌ অপ্রাসঙ্গিক অথবা রসশূন্যও নয়। তাঁর সৃষ্টির উৎসব শেষ হবার একশ’ একান্ন বছর পরে এখনও তাঁর রচনা লোকেরা পড়েন। কেবল তাই নয়, কালের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর কবিতার কোন কোনও পক্তি আমাদের ভাষায় প্রবচনের মতো গৃহীত হয়েছে। ‘একি কথা শুনি আজ….’, ‘এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে…’, ‘সম্মুখ সমর’, ‘আশার ছলনে ভুলি’, ‘কপোত-কপোতী’, ‘দাঁড়াও পথিকবর’, ‘অনিদ্রায় অনাহারে’, ‘ভিখারী রাঘব’, ‘ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা … ?’ ইত্যাদি অনুবাক্য এ রকমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। যাঁরা কোনো কালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা পড়েননি, তাঁরাও অনেকে এ কথাগুলোর অর্থ জানেন এবং নিজেদের কথাবার্তায় এগুলো ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনও বাঙালি কবির কবিতার কোনও পঙক্তি অথবা অনুবাক্য এভাবে বাংলা ভাষায় প্রবচন হিসাবে গৃহীত হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এক শতাব্দীর ব্যবধানেও কবি এখন অমর হয়ে আছেন।
কবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যুবার্ষিকীতে আজ ২৯ জুন যশোরের সাগরদাঁড়িতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মধুসূদন একাডেমির আয়োজনে সকালে মধুকবির আবক্ষ মুর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। পরে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, ভারত থেকে প্রকাশিত ‘পিলজুস’ পত্রিকার মধুসূদন সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উম্মোচন। এখানে অংশ নেবেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কবি গৌতম চৌধুরী, সমীর দে রায়সহ অন্যান্যরা।
সাজেদ রহমান : লেখক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক