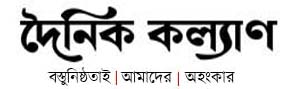সাজেদ রহমান: মহান স্বাধীনতার ৫১ বছর পর এই প্রজন্মের অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হতে পারে, তবুও সেদিন একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে নিরস্ত্র লাখো জনতা যশোর সেনানিবাস অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। একদিন নয়, পরপর ৪ দিন, ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গোটা দেশে পুরো নয় মাসে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রতিটি লড়াই ছিল সাহসে উজ্জীবিত; নির্বিকার শান্ত মৌন মানুষের ঝলসে ওঠার কাহিনীতে ভরা। তবুও এর মধ্যে কোন কোন ঘটনা আপন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে চিরকাল ইতিহাসে। যশোরের প্রতিরোধ যুদ্ধে ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের সময়কাল তেমনই একটি পর্ব, যা কখনই ম্লান হবার নয়। এই চারদিনের শিক্ষা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সাহস জুগিয়েছিল।
ঘড়ির কাঁটার মতো ঘন্টা, মিনিট কিংবা সেকেন্ডের ঘরেই ইতিহাসের কালপর্বকে বাঁধা কঠিন। কেননা ইতিহাস সামনে এগিয়ে চলে একটি ঘটনার সাথে অন্য একটি ঘটনাকে গ্রথিত করে। তাই একাত্তরে ‘যশোরের প্রতিরোধ যুদ্ধ’ শুধুমাত্র ১ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৪ এপ্রিল যশোর শহরের পতন-এই সময়কালকে নির্দেশ করে না। এটা শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন যশোরবাসী রাজপথে নেমে এসেছিলেন, আর সমাপ্তিকাল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর, যেদিন স্বাধীন বাংলার পতাকা নির্বিঘেœ উড্ডীন হয়েছিল।
মহান মুক্তিযুদ্ধে যশোরের প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তখন অস্ত্র ছিল না, সংযোগবিহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ মনোবলকে সম্বল করে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করছিলেন। এই মনোবলের ধারা বজায় ছিল বলেই পরবর্তী সময়ে হাজার হাজার ছাত্র যুবক প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ হন, গেরিলা বাহিনীর পাশাপাশি সুসংগঠিত নিয়মিত বাহিনী পাল্টা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গৌরবময় সে সব কাহিনীর অনেকটাই পত্র-পত্রিকায় এবং গ্রন্থে একের পর এক ধারণ করা হচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় প্রতিরোধ পর্বের বহু ঘটনাই আজ অপ্রকাশিত। যা জানার তাগিদ রয়েছে নতুন প্রজন্মের, যদিও ক্ষুদ্র পরিসরে তা তুলে ধরা অসম্ভব, তেমনি সম্ভব নয় তাঁদের সবাইকে সামনে আনা, যারা এই পর্বের ঘটনাবলীর নায়ক।
অবিভক্ত বাংলার প্রথম জেলা যশোরের ১৭৮১ সালে জন্ম হলেও সামরিক মানচিত্রে তা ঠাঁই পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, যখন যশোর শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ব্রিটিশরা বিশাল সেনানিবাস ও বিমান ঘাঁটি গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর সেনানিবাস ও বিমান ঘাঁটি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সেখানে অবাঙালি সৈনিকদের ‘উপনিবেশ’ গড়ে উঠে। যশোর শহরেও অবাঙালি, বিশেষ করে বিহারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমান্বয়ে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শহরের মানুষ সামরিক ও বে-সামরিক, অবাঙালিদের গভীর সখ্য যেমন লক্ষ্য করেন, তেমনি বাঙালি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তাদের বৈরী ভূমিকাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে সবার সামনে। মুসলিম লীগ নেতাদের ছত্রছায়ায় লালিত বিহারী গুন্ডাদের হাতে বাঙালি তরুণী-যুবতীদের লাঞ্চিত হবার ঘটনাও ঘটেছে অসংখ্য। এর দরুন পাকিস্তানিদের প্রতি যশোরবাসীর ক্ষোভ প্রথম সবেগে ফেঁটে পড়ে ১৯৪৮ সালের মার্চে।
ওই বছরের জানুয়ারির শেষ ভাগে ও ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতের যশোরের ছাত্র সমাজ হাতে লেখা পোষ্টার লাগান শহরের বিভিন্ন দেয়ালে। সিপিআই প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ‘ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন’-এর উদ্যোগে সমস্ত মতের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। সংগঠনটি ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ যশোর এমএম কলেজে (মাইকেল মধুসূদন কলেজ) ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে এবং তা পালিত হয়। ৭ মার্চ ছাত্ররা বের করে শোভাযাত্রা। তখনও পর্যন্ত যশোরে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের সাথে ঢাকার কোন যোগাযোগ ছিল না। পরদিন জানা যায়, ঢাকাতেও সংগ্রাম পরিষদ হয়েছে এবং ১১ মার্চ সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘট হবে। যশোরে ১১ মার্চ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ইতোপূর্বে জারি করা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে শহরে মিছিলও বের হয়। সমাবেশও হয় বিশাল আকারের। কিন্তু সমাবেশ থেকে ছাত্র-জনতা গ্রেফতার হলে ১২ মার্চ ধর্মঘট ও ১৩ মার্চ যশোর শহরে হরতাল আহবান করা হয়। হরতালের দিন শহরে মিছিল চলাকালে লাঠিচার্জ ও পুলিশের পক্ষে ফাঁকা গুলিবর্ষণ হয়, যদিও লাঠিতে বা গুলিতে কেউ গুরুতর আহত হয়নি। প্রতিবাদে হরতাল হয় ১৪ মার্চ তারিখেও। বাঙালি ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারি ছাড়াও বিপুল জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে শরিক হন এবং অত্যাচার নিপীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন চলে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। পূর্ববঙ্গ আইনসভায় যশোরের ঘটনাবলী উঠে এবং মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তাঁর বিবৃতিতে এই ঘটনা স্বীকার করে তদন্তের আশ্বাস দেন।
১৯৪৮ সালের মার্চের ঘটনায় যশোরের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের ঘটনায় আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতারা স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত হন। আর এর ধারাবাহিকতায় যশোরের ছাত্র সমাজ ও রাজনীতিকরা বায়ান্ন-উনসত্তর-একাত্তর, প্রতিটি পর্বেই নন্দিত ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হলে যশোরে এর আহবায়ক কমিটি গঠিত হয় এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ছিলেন তাঁরা এতে যোগ দেন। বায়ান্নতে যশোরের ৯৬ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়ে। ১৯৫৪ সালে সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা যশোরের জাতীয় ও প্রাদেশিক আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ১৯৫৭ সালে ন্যাপের জন্ম হওয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ন্যাপে যোগদান করলে আওয়ামী লীগ পুনঃগঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে গ্রেফতার হন যশোরের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর পর ১৯৬২ সালের ১১ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী যশোরে আসেন এবং এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করলে এর সপক্ষে সারা দেশে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। যশোর জেলা থেকে ৫ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়, যা ছিল পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ। ৬ দফা দাবি ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হয় এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার একাংশ পিডিএম গঠন করেন, যারা ৬ দফার বিরোধী। পিডিএম-এ যোগদান করেন যশোরের শহীদ অ্যাডভোকেট মসিয়ুর রহমান, মরহুম রওশন আলীর মতো নেতারা। অন্যদিকে শহীদ এ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জেলা কমিটি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। অবশ্য বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলে পিডিএম-এ যাওয়া নেতারা আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। উনসত্তরের গণআন্দোলনে সারা দেশের মধ্যে যশোরে ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে বৃহত্তর যশোরের (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল) সব কটি জাতীয় প্রাদেশিক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদে ছিলেন এ্যাডভোকেট মশিয়ুর রহমান, এ্যাডভোকেট রওশন আলী, অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল হাফিজ, কামরুজ্জামান, সোহরাব হোসেন, ইকবাল আনোয়ারুল ইসলাম, তবিবর রহমান সরদার, আবুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন, ডা. কাজী খাদেমুল ইসলাম, মঈনুদ্দিন মিয়াজী, এবিএম গোলাম মজিদ, জেকেএমএ আজিজ, শাহ হাদিউজ্জামান, আসাদুজ্জামান, সৈয়দ আতর আলী, এখলাস উদ্দিন আহমেদ, লে. মতিয়ার রহমান ও শহীদ আলী খান। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন এবং প্রতিরোধ যুদ্ধকালে প্রধানত এদের নেতৃত্বে জনগণ সংগঠিত হয়েছে এবং সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছে।